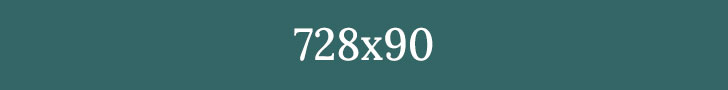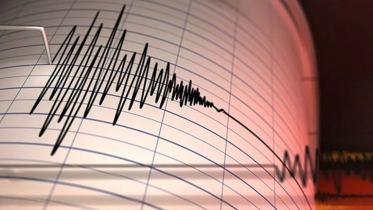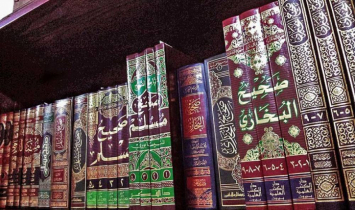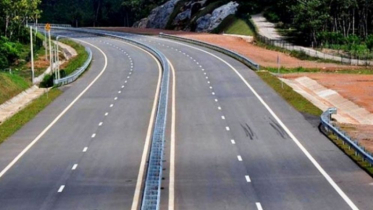প্রতীকী ছবি
চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদা, যা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তবে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় চরম বৈষম্য বিদ্যমান। নিম্নবিত্তদের চিকিৎসার জন্যে রয়েছে সরকারি হাসপাতাল, নিম্ন মধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্তদের জন্যে বেসরকারি হাসপাতাল এবং উচ্চ বিত্তদের জন্য আছে ফাইভ স্টার মানের বেসরকারি হাসপাতাল।
সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে লম্বা লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে ব্যয় করতে হয় মোটা অঙ্কের টাকা। একদিকে দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর, পদে পদে বিড়ম্বনা, অন্যদিকে ব্যয়ের চাপে নাভিশ্বাস। সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার এ চিত্র দেশের মানুষের জীবনের নিত্য বাস্তবতা।
সরকারি হাসপাতালের নাজুক অবস্থা, রোগীর তুলনায় অপর্যাপ্ত ডাক্তার, শয্যা এবং যন্ত্রপাতির যথেষ্ট সংকট রয়েছে। এ ছাড়াও সরকারি হাসপাতালে রোগীকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে চিকিৎসক ও অন্যান্য সহায়ক কর্মীদের অনীহা দেখা যায়। ফলে বাধ্য হয়েই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে এবং বিত্তশীলরা বিদেশে চলে যাচ্ছে চিকিৎসা নিতে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার মতো যে পরিমাণ হাসপাতাল, চিকিৎসক, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য দক্ষ লোকবল থাকা উচিৎ, সরকারের পক্ষ থেকে সেটা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সেই সুযোগে ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে বেসরকারি হাসপাতাল এবং চিকিৎসাকেন্দ্র। তবে এসব হাসপাতালে সেবার থেকে মুনাফা অর্জনই প্রধান লক্ষ্য।
সরকারি চিকিৎসা
সরকারি ব্যবস্থাপনায় গড়ে ওঠা হাসপাতালে চিকিৎসা বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ থাকা সাপেক্ষে রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। তবে বিনামূল্যের চিকিৎসা নিতে গিয়ে রোগীকে চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। প্রথমেই লাইন ধরে টিকিট কাটতে হয়। তারপর আবার ডাক্তার দেখাতেও দীর্ঘ সময়ে লাইন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। ডাক্তার দেখানোর পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হলে সেখানেও আবার টাকা জমা দিতে একবার লাইনে দাঁড়াতে হয়, এরপর আবার পরীক্ষার করাতেও লাইন ধরতে হয়। পরীক্ষার রিপোর্ট নেওয়ার পর ডাক্তার দেখাতে আবার লাইন দিতে হয়। উল্লেখিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে প্রায় দুই দিন লেগে যায়, যা একজন কর্মজীবী মানুষের জন্য খুবই কষ্টকর।
সরকারি হাসপাতালে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার খরচ অনেক কম। তবে সরকারি হাসপাতালে বেশিরভাগ সময়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিকল, কিংবা দক্ষ জনবলের অভাব থাকে। এমনকি রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নেই। ফলে রোগীকে অনেক টেস্ট অন্য কোনো বেসরকারি হাসপাতাল থেকে করতে হয়, যা অনেক ব্যয়বহুল।
সরকারি হাসপাতালের দক্ষ চিকিৎসক থাকলেও সেবার মান নিয়ে রোগীদের যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। অতিরিক্ত রোগীর চাপ থাকায় চিকিৎসক বেশিরভাগ সময়ে রোগীকে যথাযথ সময় দিয়ে আন্তরিকতার সাথে চিকিৎসাসেবা দিতে পারেন না কিংবা দেন না। চিকিৎসায় অন্যান্য সহায়ক লোকজনও রোগীদের প্রতি কম আন্তরিকতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবহেলা করা হয়ে থাকে।
রোগীর চাপের তুলনায় সরকারি হাসপাতালে শয্যার চরম সংকট থাকে। বেশিরভাগ সময়ে রোগী সরকারি হাসপাতালে একটা সিট পাওয়া যেন সোনার হরিণ পাওয়ার সমান। এ ছাড়াও সরকারি হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে।
বেসরকারি চিকিৎসা
সরকারি হাসপাতালের নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে দেশে গড়ে উঠেছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্যোগে বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র। বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। মুনফার পাশাপাশি তারা চিকিৎসাসেবাও দিয়ে থাকে। তবে বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসাসেবা প্রয়োজন অনুযায়ী না হয়ে, টাকা দ্বারা নির্ধারণ হয়। যার টাকা আছে, তারাই বেসরকারি চিকিৎসা পাবেন, টাকা নেই সেবাও নেই!
বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে অপেক্ষার সময় সাধারণত কম হয় এবং দ্রুত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও ভর্তি সুবিধা পাওয়া যায়। বেসরকারি হাসপাতালে আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত অবকাঠামো, পরিষ্কার-পরিছন্নতা এবং ভালো পরিবেশ থাকে। চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সকলেই রোগীর প্রতি যত্ন এবং আন্তরিকতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। পাশাপাশি রোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যা সরকারি হাসপাতালে দেখা যায় না।
বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ডাক্তার দেখাতে এক থেকে দুই হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্রুত করা গেলেও খরচ সরকারি হাসপাতালের কয়েকগুণ বেশি হয়। বেসরকারি হাসপাতালে দ্রুত শয্যা পাওয়া গেলেও ভাড়া অনেক বেশি গুনতে হয়। এ ছাড়াও অভিযোগ রয়েছে বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সামগ্রিকভাবে চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালের খরচ অনেক বেশি, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।
জরুরি চিকিৎসা
ছোট কিংবা বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালগুলোর সক্ষমতা ও অবস্থান বেশ ভালো। জরুরি বিভাগে চিকিৎসক এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থাও থাকে। যেকোনো দুর্ঘটনায় তারা তাৎক্ষণিক চিকিৎসাসেবা দেন।
বেসরকারি হাসপাতালে যেকোনো ছোট বা বড় দুর্ঘটনায় বা যেসব ক্ষেত্রে পুলিশ কেস থাকে, সেসব ক্ষেত্রে কিংবা চিকিৎসা ব্যয়ভার বহনের অনিশ্চয়তায় রোগীদের সেবা দেওয়া হয় না, কিছু কিছু সময় তাৎক্ষণিক কিছু চিকিৎসা দিয়ে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেয়।
বিশেষজ্ঞদের মতামত
সরকারি হাসপাতালগুলো সাশ্রয়ী হলেও সেখানে সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি আছে। অন্যদিকে বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে উন্নত সেবা ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া গেলেও তা বেশ ব্যয়বহুল। জনগণের জন্য এটা একটা উভয় সংকট অবস্থা।
বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সাবেক সভাপতি এবং স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব বাংলানিউজকে বলেন, মূল কথা হচ্ছে সরকার চিকিৎসাসেবা কতটুকু দেবে, কাদের দেবে? এখন বলা হচ্ছে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, কিন্তু যাদের সেবা ফ্রি পাওয়ার কথা, তারা পায় না। বেসরকারি হাসপাতালে যেহেতু সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে জানা যায় না। আবার জানলেও কিছু করার থাকে না। এ থেকে উত্তরণের উপায় হচ্ছে সুশাসন, বাজেটে যথাযথ অর্থায়ন, যাতে যারা সক্ষম না, তারা যেন চিকিৎসাসেবা পায়। এটা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়, রাষ্ট্র বা সরকার চাইলেই এটা করতে পারে।
তিনি বলেন, শুধু নীতিমালা করলেই হবে না, সেটাকে কার্যকর করতে হবে। কমিউনিটি ক্লিনিকে কী হচ্ছে? আমরা এমন কমিউনিটি ক্লিনিক চাইনি। স্বাস্থ্য শিক্ষায় কী হচ্ছে? সরকারি হাসপাতালে যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে ব্যবহার হয় না। বর্তমান সরকার রিফর্ম কমিশন করেছে, এটা কি তারা বাস্তবায়ন করবে? এগুলো ছেলে ভোলানো বিষয়। যে পর্যন্ত রাজনীতিবিদেরা এটা জনস্বার্থে করতে না চান, সে পর্যন্ত এটা হবে না। একদিনে হবে না, অন্তত ২০ বছর লাগবে, কিন্তু আমাদের শুরু করতে হবে। তারা আগ্রহী বড় বড় বিল্ডিং বানাতে, সেখান থেকে পয়সার ভাগ পাওয়া যাবে। তারা আগ্রহী বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনতে কিন্তু যন্ত্রপাতি চালাতে আগ্রহী না। যন্ত্রপাতি কিনলে সেখান থেকে তারা কমিশন পায়।
বিএমএ-এর সাবেক সভাপতি আরও বলেন, চিকিৎসকর দলবাজ হয়ে গেছেন, তাদের কখনো দলবাজ হওয়া উচিত না। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমস্যা। কোনো সরকার সমস্যা সমাধান করছে না। বেসরকারি হাসপাতালে টাকার গাট্টি নিয়ে যাবেন। তারা আপনাদের লুট করবে এবং সেটা দেখারও কেউ নেই।
কমিউনিটি ক্লিনিক হেলথ সাপোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য ডা. আবু মুহাম্মদ জাকির হোসেন বাংলানিউজকে বলেন, সরকারি হাসপাতাল দালাল পোষে না, যারা রোগীদের হাত-পা ধরে সেখানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসবে। অন্যদিকে প্রাইভেট হাসপাতালে উল্টো চিত্র দেখা যায়। সরকারি হাসপাতালেও প্রাইভেট হাসপাতালের দালাল থাকে, সরকারি হাসপাতালের ভিতর থেকেও একটা সমর্থন থাকে, তারা রোগীদের প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যায়। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা বিকেলে প্রাইভেট হাসপাতালের চেম্বারে রোগী দেখেন। দালালির এই চক্রটা একটা বড় ফ্যাক্টর।
তিনি আরও বলেন, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকের সংকট আছে, পাশাপাশি নার্স বা প্যারামেডিক যে পরিমাণ থাকার কথা, সেটাও নেই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে একজনের চিকিৎসকের অনুপাতে তিন জন নার্স, পাঁচ জন প্যারামেডিক থাকা দরকার। আমাদের সেটা নেই। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক থাকলেও যেহেতু পর্যাপ্ত নার্স, প্যারামেডিক নেই, তাই গুনগত সেবা দেওয়া যায় না। এ ছাড়াও দুটি আলাদা অধিদপ্তরের অধীনে হওয়ার কারণে চিকিৎসকদের কথা নার্সরা সবসময় শুনতেও চান না। এক্ষেত্রেও সেবার মানে ঘাটতি দেখা যায়।
স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্কার কমিশনের এই সদস্য বলেন, যেহেতু সরকারি হাসপাতালের বরাদ্দ বছর ভিত্তিক হয়, সেটা পেতেও কয়েক মাস চলে যায়, ফলে ওষুধ কিংবা অন্যান্য উপকরণের ঘাটতি দেখা যায়। গত এক বছর থেকে উন্নয়ন খাতের টাকা রিলিজ হয়নি। ফলে এখানেও একটা ঘাটতি আছে। রোগীরা ওষুধ পাচ্ছে না। এত কষ্ট করে এসে রোগীরা দেখে ওষুধ নেই, চিকিৎসককে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তারা বাধ্য হয়ে প্রাইভেট হাসপাতালে চলে যান।
বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রাইভেট হাসপাতালে যখন কোনো গর্ভবতী নারী যায়, সেখানে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব করানো হয়। এটা কোনোভাবেই ১৫ শতাংশের বেশি হওয়ার কথা না। এটা দেখার কেউ নেই। এটা যারা নিয়ন্ত্রণ করবে, তাদের ব্যাকআপ দেওয়ার কেউ নেই। প্রাইভেট হাসপাতাল যাদের, তারা অনেক ক্ষমতাবান, বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ। প্রাইভেট হাসপাতালের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার কালচার গড়ে উঠেছে। আবার সরকারি হাসপাতালের অনেকেই প্রাইভেট হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত। এজন্য প্রাইভেট হাসপাতালে তদারকি করা হয় না।